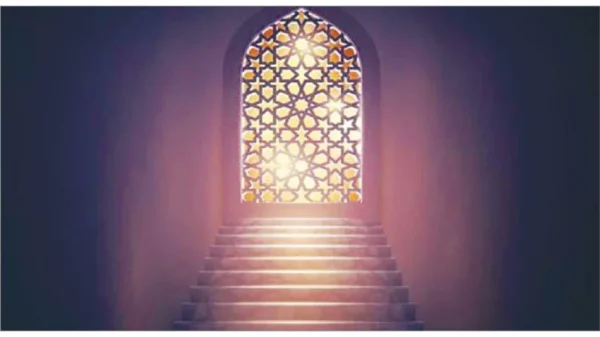বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:১১ পূর্বাহ্ন
কৃষিতে ভর্তুকি কমাতে দাতাদের চাপ

মো. মজিবুল হক মনির:
‘সবজির দাম বাড়লেও ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না কৃষক’ এই রকম শিরোনামের কোনো সংবাদ চোখে পড়লে প্রথমেই যে প্রশ্নটা আসা স্বাভাবিক তা হলো কেন? উত্তরটাও সবার জানা! উত্তরের মধ্যেই আমাদের কৃষি বিপণন ব্যবস্থাপনার একটা চরম দুর্বলতা এবং দুর্দশার চিত্র উঠে আসে। এটা সবাই জানেন যে, উৎপাদক এবং ভোক্তার মধ্যকার বিদ্যমান দূরত্ব, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য এবং অপর্যাপ্ত ও অকার্যকর বিপণন ব্যবস্থাই মূলত কৃষকের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণ। এ ধরনের সংবাদেই উল্লেখ করা থাকে যে, স্থানীয় বাজারে কৃষক যে সবজি ৫ থেকে ৬ টাকায় বিক্রি করছেন, সেই একই সবজি খানিক দূরের শহরে বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ২২ টাকায়!
ধানের বাজারের দিকে তাকালেও দৃশ্যপটের তেমন কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। বলাবাহুল্য ধানই আমাদের প্রধান কৃষিশস্য। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য, এখনো এদেশের মানুষের প্রয়োজনীয় ক্যালরির শতকরা ৭৫ শতাংশের উৎস ভাত। আর এ কারণেই প্রায় অধিকাংশ কৃষি জমিতেই চাষ হয় ধান। কিন্তু ধানচাষিরা কেমন আছেন? ২০১৮ সালে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, সে সময় মাঠ পর্যায়ে প্রতি মণ ধান উৎপাদনে কৃষকের খরচ ১২শ টাকার মতো হলেও, বিক্রি করতে হয়েছে ৮শ থেকে ৯শ টাকায়! গত বছর সরকারি পর্যায়ে প্রতি মণ ধানের ক্রয়মূল্য ১০৮০ টাকা ঠিক করে দেওয়া হলেও হাওরের অনেক কৃষকই খোলাবাজারে ধান বিক্রি করেছেন ৬শ থেকে ৮শ টাকায়, যেখানে তাদের উৎপাদন খরচ প্রতি মণে প্রায় ৭৫০ টাকা।
কৃষক যে তার উৎপাদিত কৃষিপণ্যের যথাযথ মূল্য বা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না, সেটা এখন সবারই জানা কথা, কিন্তু এর সমাধান হচ্ছে না কেন? অথচ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য আমাদের আছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের সর্বশেষ (২০২১-২২) বার্ষিক প্রতিবেদনে কিন্তু কৃষকের জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার কথাটা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনটির একেবারে শুরুর দিকে বঙ্গবন্ধুর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে ‘কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য’। কিন্তু কৃষকের জন্য সেই ন্যায্যমূল্য কি নিশ্চিত করা গেছে?
কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজের মধ্যে আছে কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সৃষ্ঠু সরবরাহে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন। বলা বাহুল্য, এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিদপ্তরকে পুরোপুরি সফল বলার উপায় নেই। অবশ্য এক্ষেত্রে অধিদপ্তরটি নিজেও বেশ কিছু সংকটের সম্মুখীন। পর্যাপ্ত লোকবলের অভাব এর অন্যতম।
কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশে, মোট শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক (৪৫.৩%) যেদেশে কৃষি খাতে সম্পৃক্ত, কৃষকের ন্যায্যমূল্য তো সেই দেশে নিশ্চিত করা জরুরি। খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার স্বার্থে এটা অন্যতম পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের কৃষি এমনিতেই নানাবিধ সংকট-সমস্যা মোকাবিলা করছে। জলবায়ু পরিবর্তন, ভর্তুকি হ্রাসে আন্তর্জাতিক নানামুখী চাপ, অকৃষি খাতে কৃষিজমির ব্যবহার বাড়ায় প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে কৃষিজমি হ্রাস, দ্রুত নগরায়ণসহ ইত্যাদি কারণে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে আছে বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতা ও হুমকি। এসব হুমকি মোকাবিলায় কৃষকের জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, কার্যকর বিপণনব্যবস্থা গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন। এজন্য স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ আশানুরূপ সাফল্য আনতে পারে। আগামী জাতীয় বাজেটে অন্তত এই দুটি উদ্যোগের আশা আমরা করতেই পারি।
দেশের বর্তমান বাস্তবতায় অবশ্য স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়াটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব কোনো কিছু নয়। উদ্যোগটি হলো কৃষি খাতে ভর্তুকি বাড়ানো, বাড়াতে না পারলেও বর্তমান কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ অন্তত অব্যাহত রাখা। যদিও কৃষিতে ভর্তুকি কমাতে আইএমএফের চাপ আছে, এই সময়ে এসে এই চাপ প্রতিরোধ করা কঠিন। কিন্তু সরকার ইচ্ছে করলে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি-অপচয় রোধ করে কৃষির জন্য ভর্তুকিটা বজায় রাখতে পারে।
বাংলাদেশের কৃষকরা সাধারণত সার ও ডিজেলের ক্ষেত্রে নগদ ভর্তুকি সহায়তা পেয়ে থাকেন। সার ও ডিজেলে ভর্তুকি বন্ধ করলে কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে, ফলে বাজারে আমাদের কৃষিপণ্যের মূল্য বাড়বে, এতে ভোক্তাদের ওপর চাপ বাড়লেও সাধারণ কৃষক কিন্তু থাকবেন ক্ষতির চক্রব্যূহেই! এক্ষেত্রে উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না যে, কৃষিতে ভর্তুকি কমানোর আন্তর্জাতিক চাপ সবসময়ই বাংলাদেশের ওপর আছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে এই চাপ দেওয়া হচ্ছে মূলত ধনী দেশগুলোর জন্য অনুকূল একটি বৈশ্বিক কৃষিবাজার তৈরি করার লক্ষ্যে। ধনী দেশগুলো ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন কৃষিতে বিরাট আকারের কৃষি ভর্তুকি দিয়ে তাদের কৃষকদের দক্ষতা বাড়িয়েছে, উন্নয়ন ঘটিয়েছে, কৃষকের সক্ষমতা বেড়েছে, তাদের বাজারব্যবস্থার কারণে কৃষকরাও সেখানে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে এই অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই উন্নত একটি দেশে ভর্তুকি বন্ধ করা আর বাংলাদেশে ভর্তুকি বন্ধ করা এক নয়। ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতে ব্যাপক পরিমাণ ভর্তুকি ও সহায়তা দিয়ে যখন তারা শিল্পোন্নত হয়েছে, তখনই ভর্তুকি কমানোর দাবি তুলছে। কারণ তারা ভর্তুকি ও সহায়তা দিয়ে তাদের নিজ নিজ দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলেছে। এখন তাদের প্রয়োজন সেই শিল্পের বাজার। তারা কোনোভাবেই চায় না স্বল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাক, এতে করে তাদের বাজার বন্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ প্রযুক্তিগতভাবে দুর্বল এবং এখনো কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যাপক প্রযুক্তি ও সফলতা নেই, সেহেতু কৃষি কাঁচামালই আমাদের বিক্রি করতে হবে। উন্নত দেশগুলো তাই চায়।
আমাদের কৃষিকে ভর্তুকি কমাতে বললেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিন্তু কৃষিতে ব্যাপক পরিমাণ ভর্তুকি দিচ্ছে। একটি হিসাব থেকে জানা যাচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১৯ সালে প্রায় ২২.২ বিলিয়ন ডলার এ খাতে ভর্তুকি দিয়েছে। একই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের খরচ প্রায় ৫০.৩ বিলয়ন ডলার।
স্বল্পমেয়াদে ভর্তুকি বাড়ানোর পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাসহ কৃষকের অনেক সমস্যা সমাধানে একটি কার্যকর ও টেকসই সমাধান হতে পারে কার্যকর কৃষি সমবায়। একটি খুব সহজ মডেল, যা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
সাধারণত চাষাবাদ থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত আমরা প্রান্তিক কৃষককে তিন ধরনের সমস্যায় পড়তে দেখি: ১) চাষের সময় পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব, ফলে উচ্চসুদে মহাজন বা দাদনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয় বা ফসল অগ্রিম বিক্রি করে রাখতে হয়, ২) উৎপাদিত ফসলের সঠিক দাম না পাওয়া, এবং ৩) মধ্যস্বত্বভোগীরা যে মুনাফা পায় তার ছিটেফোঁটাও উৎপাদক কৃষকের কাছে আসে না। এই তিনটি সমস্যাই একটি কৃষি সমবায় সমাধান করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সমবায় গঠিত হতে হবে একই ধরনের ফসল উৎপাদন করেন এমন কৃষকদের নিয়ে। পুরো কার্যক্রম শুরুর আগে দিতে হবে সমবায় পরিচালনার ওপর প্রশিক্ষণ। কৃষকদের মধ্য থেকেই কয়েকজনকে ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসতে হবে। যেহেতু এই সমবায় গঠিত হবে একেবারেই প্রান্তিক কৃষকদের নিয়ে, তাই শুরুতে সেই সমবায় প্রতিষ্ঠানকে এককালীন একটা অর্থ সহায়তা দিতে হবে। এই অর্থ দীর্ঘমেয়াদে আবার ফেরত নিয়ে নেওয়া যেতে পারে।
সমবায় গঠিত হয়ে গেলে উপরোক্ত তিনটি সমস্যার কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করতে পুরো প্রক্রিয়াটি হবে এরকম: সব সদস্য কৃষককে সমবায় থেকে চাষের জন্য জমির পরিমাণ অনুযায়ী বিনাসুদে পুঁজি সরবরাহ করা হবে। উৎপাদিত ফসল ভোক্তা পর্যায়ের মূল্যের প্রায় কাছাকাছি একটি মূল্যে সব সদস্য সমবায়ের কাছেই বিক্রি করবেন। বিক্রীত অর্থ থেকে ঋণের অর্থ কেটে রাখা হবে। সদস্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ফসল সমবায় নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শহরের বাজারে বা ভোক্তার কাছে বিক্রি করে আয় করবে। সে আয়ের ২৫% সংগঠন পরিচালনার জন্য রেখে দিয়ে বাকি মুনাফা সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।
এই সহজ ব্যবস্থাপনায় কৃষক চাষের জন্য পুঁজি পাবেন, ন্যায্যমূল্যে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারবেন, আবার ভোক্তা পর্যায়ে বা ভালো বাজারে সেই ফসল বিক্রি করে পাওয়া মুনাফাও তার কাছে ফেরত আসছে। এই ধরনের কৃষি সমবায় পরিচালনা মোটেও কঠিন বা অসম্ভব কিছু না। দিনাজপুরে ঠিক এই ধরনের একটি কৃষি সমবায়ের সঙ্গে এই লেখকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, খুব কাছ থেকে তিনি সমবায়টির কার্যক্রম দেখছেন।
দীঘন সমবায় সমিতি নামের সংগঠনটিকে কোস্ট ফাউন্ডেশন থেকে এককালীন আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়, দেওয়া হয় প্রশিক্ষণ। সমবায়টি সদস্যদের ধান চাষের জন্য বিনাসুদে ঋণ দেয়, পরে বাজারের সর্বোচ্চ দামে সেই ধান সদস্যদের কাছ থেকে কিনে নেয়, সেই ধান থেকে সংগঠনটি উন্নত মানের সুগন্ধি চাল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে মুনাফা পাচ্ছে। মুনাফা বিতরণ করা হচ্ছে সদস্যদের মধ্যে। সংগঠনটি তাদের উৎপাদিত চাল বিক্রির জন্য বিক্রয় কেন্দ্র করেছে, এখন চেষ্টা করছে অনলাইনের মাধ্যমে দেশব্যাপী তাদের চাল বিক্রির। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। এরকম সফল কৃষি সমবায় খুঁজলে আরও পাওয়া যাবে। আমাদের প্রয়োজন সমবায় আন্দোলনের। শুধু কিছু প্রকল্প নয়, প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি উপজেলায় ধীরে ধীরে একটি করে এরকম কার্যকর সমবায় প্রতিষ্ঠা করে ক্রমান্বয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে যাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করলে বা অতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে গেলে সর্বনাশ।
আগামী অর্থবছরের বাজেটে কৃষির জন্য কৃষকের জন্য, সামগ্রিকভাবে দেশের খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা জরুরি। ভুলে গেলে চলবে না, কৃষিতে ভর্তুকি কমাতে যত চাপই থাকুক মহামারী উত্তর বিশে^ ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে দেশে দেশে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। করোনাকালীন কৃষক যেমন আমাদের খাবার জোগান দিয়ে গেছেন, বর্তমান সময়েও কৃষকের ওপর আমাদের নির্ভরতা কমেনি। তাই তাদের চাপমুক্ত রাখা জরুরি।
লেখক: উন্নয়নকর্মী ও জাতিসংঘের গ্লোবাল ফার্মার্স ফোরামের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য
munir.coastbd@gmail.com
ভয়েস/আআ/সূত্র: দৈনিক দেশরূপান্তর